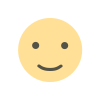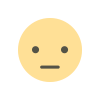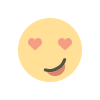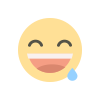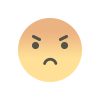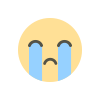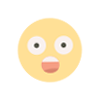অস্থিরতা এনবিআর এঃ বিরোধ কর্তৃত্ব নিয়ে

সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) বিলুপ্ত করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামে দুটি আলাদা বিভাগ তৈরির অধ্যাদেশ জারি করার পর বড় ঝাঁকুনি খেয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
এই পদক্ষেপের পর এনবিআরের কাস্টমস ও আয়কর ক্যাডারের কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন, নেতৃত্বসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। সরকার 'কৌশলে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের হাতে কর্তৃত্ব তুলে দিচ্ছে'—এমন অভিযোগ তুলে তারা আন্দোলনে নামেন। পরে এ আন্দোলনের ফলে ধাপে ধাপে সমুদ্র ও স্থলবন্দরগুলোতে প্রায় অচলাবস্থা তৈরি হয়।
এক পর্যায়ে কঠোর অবস্থান নেয় সরকার। অন্তত ৩৬ জন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত ও পাঁচজনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়—যা বাংলাদেশের রাজস্ব প্রশাসনের ইতিহাসে নজিরবিহীন।
সবমিলিয়ে প্রায় ৪ লাখ কোটি টাকা রাজস্ব আহরণকারী প্রতিষ্ঠানটির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক ও আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। অনেকেই উদ্বিগ্ন—এরপর কার ওপর আসছে খড়গ? কাকে বরখাস্ত করা হবে বা দুর্নীতি দমন কমিশন (এসিসি) তলব করছে? কাকে পাঠানো হবে দুর্গম অঞ্চলে, কিংবা অথবা করা হবে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)?
সংবাদমাধ্যম রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআরের প্রধান কার্যালয়ে কিংবা মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে খবরের সন্ধানে গেলে পরিচিত কর্মকর্তারাও দূরে সরে যান, কথা বলতে চান না। ফোনেও কথা বলতে চাইছেন না পরিচিত কর্মকর্তারা।
প্রশ্ন হলো: এনবিআরের এই অস্থিরতা কি সংস্কারে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে; নাকি কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে, সেই লড়াইয়ের ফল?
আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, সংস্কার তথা এনবিআর পৃথক করা নিয়ে সংস্থাটির কর্মকর্তাদের তেমন আপত্তি নেই। আসল বিরোধ হলো মূলত নতুন সৃষ্ট দুই বিভাগের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে।
সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তারা আপত্তি জানানোর জন্য আনুষ্ঠানিক মাধ্যম ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক বিক্ষোভে এনবিআরের কর্মকর্তারা কিছু ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।
প্রথমে যতদিন পর্যন্ত কর্মকর্তারা সংক্ষিপ্ত কর্মবিরতি বা 'কলম-বিরতি'র মতো কর্মসূচি করেছেন, তখন করদাতা, ব্যবসায়ী বা সেবাপ্রার্থীদের বড় ধরনের অসুবিধা হয়নি। সমস্যা প্রকট হয় যখন তারা আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া বা 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা দেন এবং সব কর্মকর্তাদের ঢাকায় আসতে বলেন।
গত ২৮ ও ২৯ জুন দুই দিন দেশের প্রধান বাণিজ্যদ্বার—চট্টগ্রাম বন্দর, ঢাকা কাস্টমস হাউস ও বেনাপোলের—অচল হয়ে পড়ে। এতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ শুরু হয়। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি নেতিবাচক বার্তা যায়।
সে সময় একজন ব্যবসায়ী নেতা বলেছিলেন, 'যুদ্ধ পরিস্থিতি ছাড়া এভাবে বন্দর অচল হওয়ার ঘটনা আমার জানা নেই।'
এর পর সরকারের কঠোর হওয়া ছাড়া উপায়ও ছিলো না। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার, হয়ে গেছে: বাণিজ্যে অচলাবস্থার কারণে ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির শিকার হন, আর রাষ্ট্র হারায় মূল্যবান রাজস্ব।
এনবিআরে সংস্কার কেন দরকার?
স্বাধীনতার পর পাঁচ দশক পেরিয়ে গেছে, যা একেবারে কম সময় নয়। ৪০ বছর আগেও অর্থনীতিতে বাংলাদেশের সমান অবস্থানে থাকা মালয়েশিয়া এখন ঢের এগিয়ে গেছে। অথচ বাংলাদেশ এখনও উন্নয়ন সহযোগীদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।
এর একটি বড় উদাহরণ হলো কর ব্যবস্থা: দেশের কর-জিডিপি অনুপাত ৭ শতাংশের কিছু বেশি—যা বিশ্বের সর্বনিম্ন হারগুলোর মধ্যে অন্যতম।
দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজস্ব আদায়ে অটোমেশনের কথা বলা হচ্ছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু অগ্রগতি সামান্যই। আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রক্রিয়া এখনও অনেকাংশে মানব-নির্ভর, যা করদাতাদের খরচ বাড়াচ্ছে এবং হয়রানির সুযোগ তৈরি করছে।
অন্যদিকে অসৎ কর্মকর্তাদের যোগসাজশে কর ফাঁকিবাজ ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা বিপুল রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছেন। আবার চাপ সৃষ্টি ও লবিং করে প্রভাবশালী একটি অংশ বড় অঙ্কের করছাড় আদায় করে নিচ্ছে।
এনবিআরের নিজস্ব হিসাব বলছে, সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে, তার প্রায় সমপরিমাণ রাজস্ব ছেড়ে দেয় কর অব্যাহতির (যা 'কর ব্যয়' হিসেবে পরিচিত) মাধ্যমে ।
এমন অবস্থায় বাংলাদেশের কর ব্যবস্থায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের পরামর্শ দিয়ে আসছে।
ব্যবসায়ীদেরও দাবি একই: যারা কর নীতি তৈরি করবেন, তারা কর আদায় কিংবা আদায়-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্বে থাকবেন না। অর্থাৎ নীতি থেকে বাস্তবায়নকে আলাদা করতে হবে।
সরকার সে পথেই হেঁটেছে, উদ্দেশ্য ছিল ভালো। কিন্তু গোল বাধল নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে।
বাংলাদেশে বছরের পর বছর ধরে এনবিআরের নেতৃত্ব প্রশাসন ক্যাডারের হাতেই রয়েছে। কেবল এনবিআর নয়, অন্যান্য বহু ক্যাডারের কর্তৃত্বও এই ক্যাডারের কর্মকর্তাদের হাতে, যা নিয়ে আন্তঃক্যাডার অসন্তোষ রয়েছে। বিষয়টি সরকারের জন্যও অস্বস্তিকর।
এনবিআর কর্মকর্তাদের অভিযোগ, এবারের অধ্যাদেশেও দুটি বিভাগের বিষয়ে চাতুরির আশ্রয় নিয়ে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরকে এর কর্তৃত্বে আসার পথ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সলিম রায়হান বলেন, 'রাজস্ব প্রশাসনের আধুনিকায়ন ও করভিত্তি সম্প্রসারণের জন্য কাঠামোগত সংস্কার জরুরি ছিল, কিন্তু গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছিল খণ্ডিত। এমনকি এনবিআরকে দুই ভাগে ভাগ করার পদক্ষেপটিও বিতর্ক তৈরি করেছে। সাথে কর্মকর্তাদের অসন্তোষ ও স্বচ্ছতার অভাব আস্থার সংকটকে আরও গভীর করেছে। এই পদক্ষেপগুলো কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আনার বদলে অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে।'
অধ্যাদেশ সংশোধনে কি আস্থা ফিরবে?
বৃহস্পতিবার 'রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫' উপদেষ্টা পরিষদের সভায় অনুমোদন পেয়েছে।
এতে এখন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, দুটি বিভাগের মধ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগের নেতৃত্ব অভিজ্ঞ রাজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে আসতে হবে। এর মাধ্যমে এ বিভাগে এনবিআর ক্যাডারের—কাস্টমস ও কর—কর্মকর্তাদের আসার পথ পরিষ্কার হলো। এর আগে এটি ছিল কেবল 'অগ্রাধিকার'।
তবে রাজস্ব নীতি বিভাগের ক্ষেত্রে সরকার পথটি উন্মুক্ত রেখেছে—সেখানে প্রশাসন ক্যাডার বা এনবিআর ক্যাডারের যেকোনো কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া যাবে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এর মধ্য দিয়ে এনবিআর কর্মকর্তাদের চাওয়া আংশিক হলেও পূরণ হয়েছে এবং তাদের আপত্তির যৌক্তিকতাও কিছুটা প্রমাণ হলো। যদিও কর্মকর্তাদের একটি অংশের মধ্যে এ নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়ে গেছে।
সাবেক এনবিআর সদস্য ও সংস্কার কমিটির সদস্য ফরিদ উদ্দিন বলেন, 'কর্মকর্তাদের দাবি যৌক্তিক ছিল। এনবিআরে অন্য কোনো ক্যাডারের আধিপত্য যৌক্তিক নয়। কিন্তু তারা যে প্রক্রিয়ায় আন্দোলন করেছেন, তা যৌক্তিক ছিল না। এখন আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এই দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কেননা রাজস্ব কোনো ছোটখাট বিষয় নয়।'
তবে আস্থা ফেরানো সহজ হবে না।
সাময়িক বরখাস্ত হওয়া ও বাধ্যতামূলক অবসরে যাওয়া অনেক কর্মকর্তাই সৎ হিসেবে পরিচিত। শুধু আন্দোলনের অংশ নেওয়ার কারণে এই কর্মকর্তারা যদি শাস্তির মুখে পড়েন, তাহলে তা এ খাতে শুদ্ধাচার চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করবে। ববং এতে দুর্নীতিকেই প্রকারান্তরে উৎসাহিত করা হবে।
অন্যদিকে বহুল আলোচিত কর কমিশনার মসিউর রহমানের দুর্নীতির অভিযোগে চাকুরিচ্যুতি ও আটকের ঘটনাকে স্রেফ হিমশৈলের চূড়া মনে করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান অবশ্যই দরকার। কিন্তু পাশাপাশি ভালো পারফরম্যান্সের জন্য প্রণোদনাও থাকা দরকার, যাতে রাজস্ব প্রশাসনে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি না হয়। তাদের মতে, শুধু ভয়ের সংষ্কৃতি দিয়ে রাজস্ব আদায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়ানো যাবে না।
বাজেট ঘাটতি বাড়ছে, বাড়ছে দেশি-বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরতা, শিগগিরই স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে। এমন পরিস্থিতিতে রাজস্ব বৃদ্ধি অপরিহার্য।
এজন্য শুধু কর্মকর্তাদের নয়, করদাতাদের আস্থাও ফেরাতে হবে—সৎ করদাতাদের সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি করফাঁকির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

 বাণিজ্য ও অর্থনীতি
বাণিজ্য ও অর্থনীতি